ফিরে যাওয়া
কাজী সাব্বির আহমেদ
‘ইয়ে লোয়ো কুই কেন’ – একটি বহুল প্রচলিত চীনা প্রবাদ যার অর্থ হচ্ছে ‘ফলিং লিভস সেটল অন দেয়ার রুটস’। এই প্রবাদটির গূঢ় অর্থের সাথে অভিবাসীদের জীবনচক্রের একটি প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে। অভিবাসীরা তাদের অভিবাসী জীবনের কোন এক পর্যায়ে এসে যেখান থেকে তারা এসেছিলেন সেখানে প্রত্যাবর্নের এক প্রবল তাগিদ অনুভব করেন। শেকড়ের প্রতি এই অমোঘ টান মানুষ উপেক্ষা করতে পারে না। কেউ কেউ এই ব্যাপারে অকপট। তারা তাদের গভীর হাহাকারের কথা প্রকাশ করে কিছুটা হাল্কা হতে পারেন। আবার কেউ কেউ সেটাকে প্রকাশ্যে আনতে চান না। তবে মনের গহীনে প্রত্যাবর্তনের এই আকুতি কিন্তু তারা ঠিকই টের পান। কিন্তু সেটাকে তারা আড়াল করে রাখেন নানান অজুহাতে। একজন অভিবাসীর জীবন কোনভাবেই অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতন নয়। কারণ জীবন তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় এমন কিছু বাস্তবতার মুখোমুখি যা মোকাবেলা করার কোন পূর্ব প্রস্তুতি সাধারণত তার থাকে না। কঠিন সেই বাস্তবতাকে মোকাবেলা করার ক্ষমতা একেক জনের একেক রকম। কেউ কেউ সেই প্রতিকূলতাকে জয় করে হোস্ট কান্ট্রিতে সফলতার সাথে জীবন শুরু করতে সক্ষম হন। আবার কেউ কেউ ব্যর্থ হন। তবে সবাই কিন্তু তার নিজ মাতৃভূমির প্রতি একটি টান অনুভব করেন। সেই টানকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা হয়ত মানব জাতিকে দেননি।
জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে গভীরভাবে অনুভব করেছেন অভিবাসী লেখক কামাল আল-সোলেইলি। ১৯৬৪ সালে ইয়েমেনের পোর্ট সিটি এডেন শহরে জন্ম কামাল আল-সোলেইলির। এগারো ভাইবোনের এক বিশাল পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান কামাল তার পরিবারের সাথে ১৯৬৭ সালে চলে আসেন মিশরে। সেখানে অবশ্য তার পরিবার স্থায়ী হতে পারেনি। তাদেরকে এক সময় ফিরে যেতে হয় ইয়েমেনের এডেনে। ইংল্যান্ডের নটিংহাম ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজীতে পিএইচডি করা কামাল ১৯৯৬ সালে অভিবাসী হয়ে আসেন কানাডার টরন্টো শহরে। ১৯৯৭ সালে তিনি নিজেকে যুক্ত করেন কানাডার আর্ট এবং কালচারাল বিষয়ের উপর সাংবাদিকতায়। একই সাথে শুরু করেন রায়ারসন ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম বিভাগে অধ্যপনা। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে কানাডার বিখ্যাত ‘গ্লোব এন্ড মেইল’ পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তিনি উল্লেখ করেন যে তিনি কানাডাতে আসার সাথে সাথেই নিজেকে একজন কানাডিয়ান হিসেবে ভাবতে শুরু করেন। নিজেকে অন্য যে কোন কানাডিয়ানের সমতূল্য বলেই তার বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু ২০০১ সালের ‘নাইন-ইলেভেন’-এর ঘটনার পর পরিস্থিতি পাল্টে যায় রাতারাতি। তিনি নিজেকে আবিস্কার করেন একজন ব্রাউন কানাডিয়ান হিসেবে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১৬ সালে তিনি লিখে ফেলেন তার অন্যতম বিখ্যাত বই ‘ব্রাউনঃ হোয়াট বিইং ব্রাউন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টুডে মিনস (টু এভরিওয়ান)’। এই সময় কানাডার প্রতি তার সেন্স অব বিলংগিং-এর উপলব্ধিও পাল্টে যায় তার নিজের কাছে। হোস্ট কান্ট্রি কানাডা তার অভিবাসীদেরকে নিরাপদে বাস করার যাবতীয় উপকরণ দেয়ার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে পাচ্ছে শ্রম। সেই সাথে অদৃশ্য এক দায়বদ্ধতার সামাজিক চাপে ফেলে অভিবাসীদের কাছে থেকে আদায় করে নিচ্ছে কানাডার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আনুগত্য। মাঝে মাঝে সেই দায়বদ্ধতার কথা সরাসরি স্মরণ করিয়ে দিতে অনেক ওল্ড স্টক কানাডিয়ানদের বাঁধে না। যেমন ২০১৯ সালে ‘হকি-নাইট ইন কানাডা’-এর জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ডন চেরি বলেই ফেললেন যে, ইমিগ্রান্টরা কানাডার ‘মিল্ক এন্ড হানি’-এর লোভে এদেশে এসেছে কিন্তু তারা এদেশের ভ্যালুজ-কে ধারণ করে না। মাল্টি রেসিয়াল এবং মাল্টি কালচারাল দেশ কানাডা। ফলে ‘কানাডিয়ান ভ্যালুজ’-এর কোন ডেফিনেটিভ ডেফিনিশেন কিংবা সংজ্ঞা বের করা কঠিন।
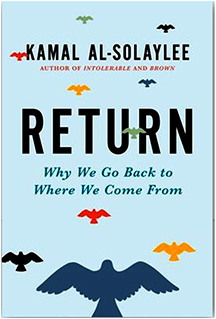
কানাডাতে আসার আগে আমি যখন সিঙ্গাপুরের ‘সিঙ্গাপুর পলিটেকনিক’-এ কাজ করতাম তখন সেখানে আমার সাথে একজন সাদা কানাডিয়ানও কাজ করতেন। তার নাম পল গ্যানুন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ১৯৭২ সালে কানাডা যখন সেই বছরের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন রাশিয়াকে হকি সামিটে পরাজিত করে তখন নাকি সমস্ত কানাডিয়ান এক সাথে উল্লাসে মেতে উঠেছিল। অর্থাৎ হকি তাদেরকে এক করেছিল। প্রকারান্তরে আইস হকি, যা কিনা নর্থ আমেরিকাতে শুধু হকি নামেই পরিচিত, হচ্ছে কানাডিয়ান ভ্যালুজ-এর অন্তর্ভূক্ত। পল গ্যানুন ছিলেন একজন ওল্ড স্টক কানাডিয়ান। তিনি হকির প্রতি আত্মার যে টান অনুভব করবেন সেটা কিন্তু একজন ইমিগ্র্যান্ট যিনি কানাডা আসার আগে কখনোই আইস হকি খেলা দেখেনি তার পক্ষে কোনভাবেই সেই একই টান অনুভব করা সম্ভব নয়। কানাডা সেটা জোর করে চাপিয়ে দিলেও নয়। তাই কামাল আল-সোলেইলি অনুভব করেন যে হোস্ট কান্ট্রি কানাডা কোনভাবেই তার অভিবাসীদের ‘সউল’ বা আত্মার দখল নিতে পারে না। অভিবাসীদের ‘সউল’ অদৃশ্য এক বাঁধনে বাঁধা পড়ে থাকে তাদের জন্মভূমির সাথে। সেই বাঁধনকেই আমরা বাংলায় নাড়ীর টান বলে থাকি। কামাল আল-সোলেইলি সেই নাড়ীর টানে তার জন্মভূমি ইয়েমেনের এডেন শহরে ফিরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করা শুরু করেন। হয়ত কখনই আর ফিরে যাওয়া হবে না তারপরও ফিরে যাওয়ার এই ব্যাকুলতাকে তিনি আমৃত্যু অনুভব করে যাবেন। অন্যান্য অভিবাসীরা এই ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কি ভাবেন সেটা খুঁজতে তিনি বেরিয়ে পড়েন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। তিনি অবাক হয়ে দেখতে পান যে তাদের ভিতরও একই অনুভূতি বিরাজমান। ‘নাইন-ইলেভেন’-এর ঘটনা তাকে তার নিজ জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে প্রথমবারের মতন ভাবিয়েছিল। সেই ঘটনার বিশ বছর পর ২০২১ সালে তিনি তার ভাবনাগুলিকে গুছিয়ে লিখে ‘রিটার্নঃ হোয়াই উই গো ব্যাক টু হোয়্যার উই কাম ফ্রম’ নামক বই আকারে প্রকাশ করেন। বইটি প্রকাশ করে হারপার-কলিন্স, কানাডা।
ফিরে যাওয়ার এই তাগিদ আমরা দেখতে পাই ওমের আজিজের ভেতরও। ‘নাইন-ইলেভেন’-এর সময় কালে টরন্টো শহরে বেড়ে উঠা পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত ওমের আজিজের কাছে মনে হয়েছে কানাডাতে অভিবাসীদের জন্য অ্যাসিমিলেশন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের কারণে তিনি এক সময় তার ধর্মীয় বিশ্বাসকে পাশে সরিয়ে অন্যান্য টিন-এজার কিংবা ইয়াং এডাল্টের মতন অ্যালকোহল এবং ড্রাগসের দিকে পা বাড়ান। তিনি মনে করেন যে তার এই ‘উদার মনোবৃত্তি’ তাকে এদেশের ‘কালচার’ এবং ‘ভ্যালুজ’-এর সাথে অ্যাসিমিলেট করতে সাহায্য করবে। কিন্তু সেটা ছিল একটি বিভ্রম। এক সময় হাই স্কুলে পড়ালেখার প্রতি অনীহা জন্মালেও পরবর্তীতে কঠোর অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি একাডেমিক সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু ক্যারিয়ার জীবনে তিনি স্পষ্টতই দেখতে পান যে বাদামী চামড়ার কারণে তিনি প্রতি পদে পদে নাজেহাল হচ্ছেন। এই কারণে প্রাইম মিনিস্টারের ফরেন পলিসি অ্যাডভাইজার প্যানেলে থাকা অবস্থায় তিনি কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেন। এক সময় তিনি ডিপ্রেশনের শিকার হন। জীবনের এই কঠিন সময়ে তিনি প্রবলভাবে অনুভব করেন পাকিস্তানের পেশোয়ার শহরে বেড়াতে যাওয়ার যেখান থেকে তার বাবা এদেশে এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। ‘ব্রাউন বয়ঃ আ মেমোয়ার’ নামক বইটিতে ওমের আজিজ তার নিজ জীবনের কাহিনী তুলে ধরেছেন এবং সেই সাথে ব্যক্ত করেছেন এমন এক শহরে ফেরত যাওয়ার তীব্র আকুতি যেখানে বাস করে তার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনেরা – যে শহর কিংবা যে দেশ কিংবা সেই আত্মীয়-স্বজনদেরকে তিনি আগে কখনো চোখে দেখেননি। একেই বলে হয়ত নাড়ীর টান।
‘নাইন-ইলেভেন’ ঘটনার ঠিক পাঁচ বছর পর অর্থাৎ ২০০৬ সালে আমি আমার পরিবারসহ সিঙ্গাপুর থেকে একেবারে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে আসি কানাডার টরন্টো শহরে। সাত ছুঁই ছুঁই বয়সের একমাত্র পুত্র সন্তানকে নিয়ে আমাদের ছোট্ট পরিবার। আমি সিঙ্গাপুরের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়ণের একটি প্রজেক্টে সিনিয়র সফটওয়্যার প্রকৌশলী আর আমার স্ত্রী জন হপকিন্স হসপিটালের সিঙ্গাপুর শাখায় ক্যান্সার সায়েন্টিস্ট হিসেবে কর্মরত। আমাদের সন্তান সবে প্রাইমারি ওয়ানের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা শেষ করেছে। জীবনের এই পর্যায়ে অভিবাসন ভিসা নিয়ে টরন্টোতে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেয়াটা খুব একটা সহজ ছিল না আমাদের জন্য। জোরালো কোন কারণ ছাড়া নিশ্চিত জীবন ছেড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি দেশে অভিবাসী হিসেবে কেউ হুট করে চলে আসে না। আমাদের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য ছিল। আপনি যদি আমাদের মতন সদ্য আসা কোন অভিবাসী দম্পতিকে প্রশ্ন করেন কেন এসেছেন কানাডাতে তবে সিংহভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর পাবেন যে তারা তাদের সন্তানদের উন্নত এবং নিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য এসেছেন। তার সাথে হয়ত যোগ হবে এদেশের উন্নত জীবন ব্যবস্থা, বিনামূল্যে বিশ্বমানের চিকিৎসার সুবিধা, সামাজিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বাক স্বাধীনতা কিংবা ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরাও আর দশটি অভিবাসী পরিবার যে সব কারণে কানাডাতে আসে ঠিক সেই সব কারণেই এদেশে এসেছি। একজন অভিবাসী যখন তার হোস্ট কান্ট্রিতে এসে নতুন জীবন শুরু করেন তখন কিন্তু তাকে অনেকটা কেঁচে গণ্ডূষ করেই জীবন শুরু করতে হয়। অর্থাৎ অতীতে যা কিছু তিনি অর্জন করেছিলেন তার অনেকটাই তাকে ত্যাগ করতে হয়। সাথে করে তিনি শুধু আনতে পারেন নগদ কিছু অর্থ সম্পদ আর তার অর্জিত বিদ্যাশিক্ষা। স্কিল ক্যাটেগরিতে আসা অভিবাসীদের জন্য এই বিদ্যাশিক্ষাই হয়ে উঠে তার জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ কিংবা যুদ্ধ জয়ের হাতিয়ার। আমার মতন ক্যারিয়ারের মিড-লেভেলে থাকা অবস্থায় নতুন একটি দেশে এসে একই ক্যারিয়ারের একটি চাকরী বাগিয়ে ফেলা অনেকটা লটারি জয়েরই সামিল। একজন অভিবাসীর জন্য নতুন দেশে এসে ক্যারিয়ার গড়ে তোলা একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। কিন্তু তারপরও কেন এদেশে আসা? আসলে এই প্রশ্নের কোন সহজ জবাব নেই।
অভিবাসন প্রক্রিয়াটা অনেকটা একটি ম্যাচিউরড গাছকে শিকড়সহ উপড়ে তুলে একস্থান থেকে অন্য একস্থানে রোপণ করার মতন। গাছের ক্ষেত্রেও যেমন একটা শক কাজ করে, তার যেমন সময় লাগে নিজেকে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে আবারও নতুন পাতা ছড়াতে, মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম অনুভূতি কাজ করে। অভিবাসন একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া কারণ এখানে কিছু পাওয়ার জন্য আমাদেরকে ছাড় দিতে হয় অনেককিছু। সে কারণে প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের মনে একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় যা তারা অনেক সময় লুকিয়ে রাখতে চায়, এমনকি নিজের কাছ থেকেও। আমি যে বছর কানাডাতে আসি সেই বছরই মুক্তি পায় ‘নেমসেক’ – ঝুম্পা লাহিড়ীর উপন্যাস থেকে মিরা নাইর-এর নির্দেশনায় নির্মিত একটি হৃদয়স্পর্শী মুভি। কলকাতার মেয়ে অসীমা এমআইটি-তে অধ্যয়নরত বাঙালী ছেলে অশোককে বিয়ে করে পাড়ি জমায় আমেরিকাতে। সেখানে শুরু হয় তাদের সংসার, তাদের ছেলের নামকরণ করা হয় বিখ্যাত রুশ উপন্যাসিক নিকোলাস গগলের নামানুসারে ‘গগল’। সেই গগলের চোখে দেখানো হয় আমেরিকার সমাজে তার খাপ খাওয়ানোর বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তার বাবা মার আকুলতা, তার বোনের খুব সহজেই এই জীবনকে মানিয়ে নেয়া। সহজ কথায় এক বাঙালী অভিবাসী পরিবারের ফেলে আসা দেশকে নিয়ে তাদের টানাপোড়েনকে জীবন্ত করে দেখানো হয়েছে এই মুভিতে। আমি নিজে যেহেতু সেই সময় মাত্র অভিবাসী হয়ে কানাডাতে এসেছি, সেই কারণে হয়ত মুভিটি আমাকে বেশ গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ‘নেমসেক’-এর দর্পণে যেন নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছিলাম।
একজন অভিবাসী মানুষের জন্য একটি অপরিচিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়াটা অবশ্যই কোন সহজ ব্যাপার নয়। তাকে প্রথমেই যে জিনিষটিকে বিসর্জন দিতে হয় সেটি হলো তার নিজস্ব চেনা পরিচিত দেশ এবং সমাজ। যে দেশ এবং সমাজের মাঝে সে বড় হয়েছে, গড়ে উঠেছে তার মূল্যবোধ এবং দৃঢ় হয়েছে তার মানসিক মনোবল, একে একে এই সবগুলোকেই তাকে খোয়াতে হয় যখন সে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে অজানা অচেনা অন্য একটি দেশে পাড়ি জমায়। তার জন্য তখন প্রথম ও প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় অ্যাসিমিলেশন। অর্থাৎ নতুন দেশটির সমাজ ব্যবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া। কারণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন মানুষই জীবন যাপন করতে পারে না। নতুন দেশের সমাজ ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য যে বিষয়গুলি বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে তার ভিতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতিগত প্রভেদ, ভাষাগত সমস্যা এবং ধর্মীয় বিধিনিষেধ। তবে সব ইমিগ্র্যান্টকেই যে এই তিনটি বাঁধাকেই অতিক্রম করতে হবে তা কিন্তু নয়। যেমন আইরিশ কোন নাগরিক যদি কানাডার টরন্টোতে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসতে চায় তবে হয়ত এই তিনটি বাঁধার একটিকেও তাকে অতিক্রম করতে হবে না। অন্যদিকে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আসা প্রায় প্রতিটি ইমিগ্র্যান্টকেই আবার এই তিনটি বাঁধার সব গুলোরই সম্মুখীন হতে হবে। ইস্ট ইউরোপীয়ানদের ক্ষেত্রে হয়ত ভাষাটাই একটু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় কারণ জাতিগত কিংবা ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতে তারা এখানকার ওল্ডস্টক সাদা কানাডিয়ানদের সমতুল্য। সেজন্য তাদেরকে অন্যান্য ইমিগ্র্যান্টদের মতন ‘ভিজিবল মাইনরিটি’-এর কাতারে ফেলা হয় না। অ্যাসিমিলেশন নামক এই সমীকরণের আরেকটি জটিল অংশ হচ্ছে নতুন ইমিগ্র্যান্ট গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সেই দেশের নীতিমালা এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ। এ ক্ষেত্রে ইমিগ্র্যান্ট গ্রহণকারী দেশগুলি সাধারণত হয় ‘মেল্টিং পট’ নয় ‘মোজাইক’ নীতি গ্রহণ করে থাকে। অ্যাসিমিলেশনের ব্যাপারে কানাডার নীতি হচ্ছে মোজাইক, অর্থাৎ সবাই নিজ নিজ কালচারকে এখানে যথাযথভাবে পালন করে যেতে পারবে। এই মোজাইক নীতির কারণে কানাডা গোড়া থেকেই নিজেকে একটি সত্যিকারের মাল্টি-কালচারাল দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছে। ফলে এদেশে বিশেষ করে টরন্টোতে আমরা দেখতে পাই মোজাইক দানার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন কালচারের এবং বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষেরা। সবাই সবার কালচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানের কারণে টরন্টো হয়ে উঠেছে ইমিগ্র্যান্টদের কাছে সবচেয়ে পছন্দের শহর। তবে এ কথা সত্য যে টরন্টো বাদে অন্যান্য শহরগুলিতে ইমিগ্র্যান্ট অথবা ভিসিবল মাইনোরিটিদের বসবাসের জন্য অনেক সময় কিছুটা চ্যালেঞ্জিং। ২০২১ সালে কানাডার অন্টারিও প্রদেশের লন্ডন শহরে ২০ বছর বয়স্ক এক সাদা কানাডিয়ান যুবক পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এক ফ্যামিলির চারজন সদস্যকে গাড়ীচাপা দিয়ে হত্যা করেছে। এই হামলায় শুধুমাত্র নয় বছর বয়স্ক এক বালক প্রাণে বেঁচে গেলেও সে ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়। শুধুমাত্র ইসলামবিদ্বেষের কারণে সেই যুবকটি এই হত্যাকান্ডটি চালায়। নর্থ আমেরিকাতে যে শুধু মুসলিম ইমিগ্র্যান্টরা বিদ্বেষের শিকার হয় তা কিন্তু নয়, একই বছরে অর্থাৎ ২০২১ সালে আমেরিকার আটলান্টা সিটিতে ২১ বছর বয়স্ক এক সাদা আমেরিকান ৮ জন এশিয়ানকে গুলি করে হত্যা করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে নর্থ আমেরিকার চাইনিজ কমিউনিটি ‘স্টপ এশিয়ান হেইট’ প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় নেমে আসে। অর্থাৎ ‘ভিসিবল মাইনরিটি’-দের জন্য অ্যাসিমিলেশনের চ্যালেঞ্জ আরও বেশী।
সদ্য আসা অভিবাসীদের জন্য প্রথম এবং প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ক্যারিয়ার গঠন। আমাদের বাংলাদেশী কমিউনিটির অনেকেই এদেশে এসে নিজের মূল পেশার সাথে নিজেকে যুক্ত করতে ব্যর্থ হন, বিশেষ করে যারা দেশে ডাক্তার, ল’ইয়ার কিংবা আর্কিটেক্ট ছিলেন। কারণ তাদেরকে পরীক্ষা দিয়ে এদেশের প্রফেশনাল লাইসেন্স নিতে হয়। পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করাও অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়ায় একটি বড় চ্যালেঞ্জ। একটা ডিসেন্ট ক্যারিয়ার গড়ে তোলার জন্য যে ‘গেম-প্ল্যান’-এর দরকার সেটা হয়ত নতুন ইমিগ্র্যান্টদের কাছে কিছুটা থাকে অজানা, আর বাকীটা থাকে ‘ক্যাচ-টুয়েন্টি-টু’-এর মতন অধরা। কারণ মাস গেলেই যখন বাড়ী ভাড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের বিল দৈত্যের আকৃতি নিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তাদের অনেকেরই পক্ষে আর ক্যারিয়ার গঠনের দিকে তাকানোর সময় থাকে না। হাতের কাছে যা কিছু একটা পাওয়া যায় এই মানসিকতাতেই তখন তারা একটা সার্ভাইভাল জব খুঁজতে থাকে এবং এক সময় তারা হয়ত একটা ‘প্রিকারেয়াস জব’ পেয়েও যায়। জীবনের প্রয়োজনে তাদেরকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই জব করে যেতে হয় যেখানে তারা কখনই কাজ করে তৃপ্তি পান না। ফলে অনেকেই বিষণ্ণতার শিকার হন এবং দেশের কথা মনে করে নস্টালজিয়ায় ভুগেন। কানাডার জীবনটা তখন তাদের কাছে অর্থহীন মনে হয় এবং দেশে ফিরে যাওয়ার এক অলীক স্বপ্নে তারা বিভোর থাকেন। আবার অনেকে এদেশে এসে জীবনটাকে নতুন করে সাজানোর সুযোগ পেয়ে সেটাকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগান। এদেশের সবকিছুর সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করে জীবনটাকে উপভোগ্য করে তুলেন। অনেকে এখানে এসে এমন সব পেশার সাথে জড়িয়ে যান যা তারা হয়ত দেশে থাকলে কখনই সেটা করতেন না। এর মধ্যে ট্যাক্সি চালানো, ড্রাইভিং শেখানো কিংবা দেশে টাকা পাঠানোর সার্ভিস হচ্ছে অন্যতম। তবে অনেকে আবার বাড়ী বেচাকেনার লাইসেন্স নিয়ে রিয়েলেটরের ব্যবসায় নাম লিখান। কেউ কেউ গ্রোসারী কিংবা রেস্টুরেন্টের ব্যবসা খুলে বসেন। বাংলাদেশী অধ্যুষিত ড্যানফোর্থ এবং ভিক্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন এলাকায় এই সব গ্রোসারী কিংবা রেস্টুরেন্ট বেশী চোখে পড়ে। বাংলাদেশীরা এদেশে এসে বিচিত্র সব পেশায় জড়িয়ে গেছেন এবং অনেকে আবার সেই সব পেশায় বেশ সুনামও কুড়িয়েছেন। বাংলাদেশী মিষ্টান্ন দিয়ে মিসিসাগা এবং ব্র্যামটনের ভারতীয় কমিউনিটির বাজার দখল করে নেয়া ব্যবসায়ী যেমন রয়েছেন তেমনি আবার ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অন্টারিও-এর প্রেসিডেন্টের পদও অলংকৃত করা একাডেমিশিয়ানও রয়েছেন আমাদের কমিউনিটিতে। তবে আমার দৃষ্টিতে এদেশের মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণের হার অন্যান্য ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটির চেয়ে একবারে অপ্রতুল। অন্টারিও-এর এমপিপি ডলি বেগম ছাড়া আর কোন বাংলাদেশী কানাডিয়ান এদেশের রাজনীতির বড় কোন পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেননি এখনও। একজন আবার কোন রকম হোম ওয়ার্ক না করেই সরাসরি টরন্টোর মেয়র পদে দাঁড়িয়ে আমাদের কমিউনিটিকে কী বার্তা দিতে চেয়েছিলেন তা এখনও আমার কাছে বোধগম্য হয়নি। অনেকে হয়ত এদেশের মূলধারার রাজনীতির হালচাল না বুঝেই শুধুমাত্র বাংলাদেশী কানাডিয়ানদের ভোট ব্যাংককে পুঁজি করে যে কোন দলের কাছ থেকে নমিনেশন পেতে আগ্রহী। কিন্তু আমাদের একটি কথা মনে রাখা উচিৎ যে কোন ক্যারিয়ারেই শর্ট কাট কোন রাস্তা নেই। পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় এই দুটো কোয়ালিটি দ্বারাই ক্যারিয়ারে সফল হওয়া সম্ভব কানাডাতে।
ক্যারিয়ারের পর যে জিনিষটি নিয়ে অভিবাসীরা সবচেয়ে বেশী বিপাকে পড়ে সেটা হচ্ছে হোস্ট কান্ট্রির সোশ্যাল ভ্যালুজ-এর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে। অনেক সময় এই নিয়ে নিজেদের কমিউনিটির ভেতর মত বিরোধের সৃষ্টি হয় কে কতখানি ‘কানাডিয়ান লাইফস্টাইল’ তাদের জীবনে মেনে চলেন এই নিয়ে। তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে এইসব সোশ্যাল ভ্যালুজের কোন ডেফিনেটিভ ডেফিনেশন নেই। তাই উইল ফারগুসন এবং ইয়েন ফারগুসন ‘হাউ টু বি আ কানাডিয়ান’ শিরোনামের একটি স্যাটেয়ার ধর্মী বই লিখেছেন যা কিনা মূলত ওল্ড স্টক কানাডিয়ানদের উদ্দেশ্য করেই লেখা। উল্লেখ্য লেখকদ্বয় উভয়েই ‘স্টিফেন লিকক মেডেল ফর হিউমার’ পদকপ্রাপ্ত লেখক। বিশাল কানাডার এক প্রদেশের কালচারের সাথে অন্য প্রদেশের কালচারের প্রভেদ থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলে কোন কালচারটি কানাডিয়ান কালচার হিসেবে বিবেচিত হবে সেটা তর্কসাপেক্ষ। আমরা যখন ২০০৬ সালে কানাডাতে আসি তখন কনজারভেটিভ দল ক্ষমতায় ছিল। লক্ষ্য করে দেখেছি যে অনেক বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্ট কনজারভেটিভ পার্টির মতাদর্শ কিংবা ম্যান্ডেটকেই ‘কানাডিয়ান
লাইফস্টাইল’ বলে ধরে নিয়ে নিজেদেরকে সেইভাবে মোল্ড করে ফেলেছেন। মানুষ যেমন তার নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা পছন্দ করেন না, তারাও তেমনি এখানকার অর্থনৈতিক কিংবা সমাজ ব্যবস্থার কোন সমালোচনা সহজভাবে নিতে পারেন না। তারা কোন ধরনের যুক্তিকে না মেনে প্রথমেই সমালোচনাকারীকে আঘাত করে থাকেন এই বলে যে, আপনি যদি এদের মতন করে চলতে না পারেন তবে এদেশে এসেছেন কেন। তারা ভুলে যান যে ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে এদেশে আসার কারণে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কিংবা ইকনমিক পলিসি নিয়ে কোন সমালোচনা করা যাবে না এই মর্মে এদেশে কোন আইন নেই।
নিঃসঙ্গতা এবং তারই হাত ধরে আসা ডিপ্রেশন হচ্ছে কানাডার একটি বহুল আলোচিত সামাজিক সমস্যা। ওল্ডহোমগুলিতে গেলে দেখা যায় অসহায় বৃদ্ধদের করুণ দশা। তারা যেন জীবিত থেকেও মৃত। অভিবাসীরাও সেই সমস্যা থেকে মুক্ত নন। বৃদ্ধ বয়সে অনেক বাংলাদেশী অভিবাসী দেশে ফিরে যেতে চান এই ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়। কিন্তু দেশে ফিরে গেলে কানাডার উন্নত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হতে হবে সেই আশঙ্কায় দেশে আর ফেরা হয় না। অনেকেই দেশে ফেরত গিয়েও সেখানে আর টিকতে পারেন না। কারণ আমরা যে বাংলাদেশকে ছেড়ে এসেছি সেই বাংলাদেশেরও অনেক পরিবর্তন এসেছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে। নিজের পরিচিত দেশ এবং সেই সাথে আপনজনও হয়ে উঠে অপরিচিত। ফলে বেশীরভাগ মানুষই আবার ফিরে আসে তাদের হোস্ট কান্ট্রি কানাডাতে। এ যেন অদ্ভুত এক গোলকধাঁধায় বাঁধা পড়া এক জীবন। না ঘরকা না ঘাটকা। কানাডার একটি শীর্ষ ব্যাংকে কর্মরত আমার পরিচিত একজনের সহকর্মী ছিলেন কলকাতার এক বাঙালী ভদ্রলোক। সেই বাঙালী ভদ্রলোক কলকাতা থেকে প্রথমে কয়েকমাসের জন্য একটি প্রজেক্টের কাজে টরন্টোতে আসেন। অন্য সবার দেখাদেখি তিনিও এক সময় পার্মানেন্ট রেসিডেন্সির জন্য আবেদন করে কানাডাতে স্থায়ী হয়ে যান। কিন্তু মন থেকে তিনি কলকাতার জীবনকে মুছতে পারেননি। তাই কাজের ফাঁকে ডাউনটাউনের উঁচু অফিস বিল্ডিং-এর নীচে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে আমার পরিচিত সেইজনকে বলেছিলেন, ‘দাদা, এই জীবনে কোন চার্ম খুঁজে পেলাম না’। দিনশেষে এই মূল্যটাকেই বুঝি চুকোতে হয় সব অভিবাসীকে।
কাজী সাব্বির আহমেদ
কলাম লেখক । টরন্টো




